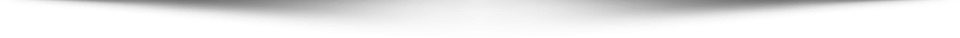সম্প্রতি এশিয়া প্যাসিফিক ডিফেন্স রিপোর্টার পত্রিকার সম্পাদক কিম বার্গম্যান সরকারি আমন্ত্রণে ঘুরে এসেছেন চীন। সফর করেছেন সিনচিয়াং উইগুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। ঘুরে ফিরে দেখেছেন কাশগর, উরুমছি ও ইলি। নিজের পত্রিকায় লিখেছেন এক নতুন সিনচিয়াংয়ের জয়যাত্রার গল্প। তার প্রতিবেদনটির চুম্বকাংশ তুলে ধরা হলো পাঠকদের জন্য।
চীনের দূর পশ্চিমে সিনচিয়াং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। সুপ্রাচীনকাল থেকেই শত শত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুটে পরিপূর্ণ এটি। একসঙ্গে এগুলোই ছিল ‘সিল্ক রোড’ ওরফে রেশমপথ। এ নাম আজও পরিচিত বিশ্বে। যদিও একসময়কার ধুলোমাখা সরু পথের সমাহারে এখন জায়গা করে নিয়েছে আধুনিক মহাসড়ক ও পণ্যবাহী রেললাইন।
সিনচিয়াং বিশাল। প্রায় অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের সমান। এখানকার আড়াই কোটি মানুষের মধ্যে অর্ধেকই প্রাচীন তুর্কি ভাষাভাষী উইগুর জনগোষ্ঠী। বাকি ১ কোটি ২০ লাখের মতো আছে যারা নতুন বসতি স্থাপনকারী হান চীনা। কাজাখসহ আরও কয়েকটি ছোট জাতিগোষ্ঠীও আছে এখানে।
প্রায় ২,৩০০ বছর আগে গড়ে ওঠা সিল্ক রোড করিডরটি চীনকে যুক্ত করেছিল এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও রাশিয়ার সঙ্গে। আজ সেটি নতুন রূপে বিস্তৃত হচ্ছে একুশ শতকের প্রযুক্তির মাধ্যমে—বেইজিংয়ের ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ’ (বিআরআই) প্রকল্পের আওতায়। প্রায় ১৫০টি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে রেলপথ, সড়ক ও বন্দরসহ এক বিশাল অবকাঠামো নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে এর অধীনে।
এই বিআরআই প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সিনচিয়াংয়ের রাজধানী উরুমছি। যার আরেক নাম ‘আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর’। গত সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের একটি দল সেখানে আট দিনের সফরে যায়। শহরজুড়ে তখন সিনচিয়াং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের ৭০ বছর পূর্তির পোস্টার লাগানো।
উরুমছিকে মধ্য এশিয়ার কেন্দ্র বললেই বোঝা যাবে না, যে শহরটি আসলে ঠিক কতটা কেন্দ্রে আছে। ভৌগোলিকভাবে এটি পৃথিবীর সেই বিন্দু, যা সমুদ্র থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। কাছের সমুদ্র উপকূল এখান থেকে এটি প্রায় ২,৬৪৫ কিলোমিটার দূরে। তাই বলে এটাকে আবার ‘স্থলবেষ্টি’ বলাটাও ভুল হবে।
একসময় ছোট ও নীরব বাণিজ্য নগরী উরুমছি এখন ৪০ লাখ বাসিন্দার এক ব্যস্ত শহর, যেখান থেকে সড়ক ও রেলপথ ছড়িয়ে গেছে বাকি সব অঞ্চলে। ২০২৫ সালের এপ্রিলেই চালু হয়েছে এর নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ইতোমধ্যে বিশাল রেলইয়ার্ড থেকে প্রতিদিন গড়ে তিনটি মালবাহী ট্রেন ইউরোপের পথে রওনা দেয়। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। কারণ বিআরআই–এর আওতায় মধ্য এশিয়ার প্রতিবেশী ইসলামিক দেশগুলো—যেমন কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, এমনকি আফগানিস্তানেও নতুন অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে।
ইতিহাসে এই অঞ্চল বহুবার বড় শক্তিগুলোর দ্বন্দ্বের উর্বর ক্ষেত্র ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে এটি ছিল ‘গ্রেট গেম’ নামে পরিচিত এক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু—যেখানে মুখোমুখি হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও রুশ সাম্রাজ্য।
তখন ব্রিটিশরা ভাবত, সিনচিয়াং, আফগানিস্তান ও টিবেটের মতো অঞ্চলগুলো তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা-ঢাল, যাতে রাশিয়া ভারতের দিকে স্থলপথে আগ্রাসন চালাতে না পারে। পরে দেখা গেল, সেই ভয় ছিল অতিরঞ্জিত। কিন্তু রাশিয়া-ভীতি তখন এমন ছিল যে, অস্ট্রেলিয়াতেও নানা দুর্গ তৈরি করা হয় সম্ভাব্য ‘জারবাদী’ আক্রমণ ঠেকাতে।
তখন আফিম যুদ্ধ, তাইপিং বিদ্রোহসহ নানা অভ্যন্তরীণ সংকটে চীন এমনিতেই বিপর্যস্ত। নিজের মাটিতে চলা ওই শক্তির লড়াইটা চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার ছিল না। আজও মধ্য এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের এই প্রতিযোগিতা চলছে, আর সেই কারণেই বেইজিংয়ের কাছে সিনচিয়াংয়ের নিরাপত্তা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়।
রাশিয়া ও চীনের মধ্যে মধ্য এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের এক শান্ত প্রতিযোগিতা চলছে—যেখানে চীন স্পষ্টতই এগিয়ে। তবে সিনচিয়াংয়ের জন্য বড় হুমকি এসেছে জঙ্গিবাদী চরমপন্থা থেকে, যে ব্যাপারটা পশ্চিমা দুনিয়া ভালোমতো বুঝতেই পারে না।
মিডিয়া সফরের একটি বড় অংশ ছিল বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প নিয়ে; আরেকটি অংশ ছিল উইগুর জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে। দুটোই আসলে একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।
গত এক দশকে উইগুরদের প্রতি চীনের আচরণ নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায় বেশ সমালোচনা হয়েছে। ২০১৪ ও ২০১৭ সালের নিরাপত্তা অভিযানকে কেন্দ্র করে এসব অভিযোগ ওঠে। কিন্তু প্রায়শই প্রতিবেদনে বাদ পড়ে যায় এই তথ্য যে, এসব অভিযান মূলত একের পর এক সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়াতেই চালানো হয়েছিল। হামলাগুলো চালিয়েছিল ইস্ট তুর্কিস্তান ইন্ডিপেনডেন্স মুভমেন্ট, ইসলামিক স্টেট–খোরাসান এবং আরও কিছু গোপন সংগঠন।
সফরের বড় অংশই ছিল সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক। উইগুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন বা ইসলামি আলেমদের সঙ্গে আলাপ। তবে নিরাপত্তা-সম্পর্কিত ব্রিফিংগুলোতে বোঝা গেল সমস্যার প্রকৃত ব্যাপ্তি। দলটি পরিদর্শন করে ‘এক্সিবিশন অব কাউন্টারটেরোরিজম অ্যান্ড ডির্যাডিকালাইজেশন ইন সিনচিয়াং’।—উরুমছিতে অবস্থিত এ প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত নয়। কারণ, সেখানে গত ২০ বছরের নানা সন্ত্রাসী হামলার ভিডিও ও উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্র দেখানো হচ্ছিল। পশ্চিমা গণমাধ্যমের দৃষ্টিসীমা সীমিত, তাই এসবের কিছুই সেখানকার সংবাদে আসে না।
আমরা সবাই ৯/১১ হামলার কথা জানি। প্যারিসের বাতাকলান থিয়েটার (২০১৫), লন্ডন ব্রিজ (২০১৭), কিংবা মাদ্রিদের ট্রেন বোমা হামলা (২০০৪)—সবই বহুল প্রচারিত। কিন্তু কে জানে উরুমছির দাঙ্গা (২০০৯, ১৯৭ নিহত), কুনমিং রেলওয়ে স্টেশন হামলা (২০১৪, ৩১ নিহত), কিংবা ২০১২ সালে হোথান থেকে থিয়েনচিনগামী বিমান অপহরণের চেষ্টা সম্পর্কে? এ কারণেই উরুমছি বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পরীক্ষাটা ছিল লেখকের জীবনে দেখা সবচেয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।
২০১৩ সালের অক্টোবরেও জঙ্গিরা বেইজিংয়ের থিয়েনআনমেন স্কয়ারে জনতার ওপর গাড়ি তুলে দুইজনকে হত্যা করে এবং গাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনাটি রাজধানীতে ঘটেছিল ও টেলিভিশনে ধরা পড়েছিল বলে আন্তর্জাতিকভাবে কিছুটা প্রচার পায়। চীনা কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রতিটি সন্ত্রাসী ঘটনার বিস্তারিত তারা প্রকাশ করেছে। তবে এসবে পশ্চিমা মিডিয়ার অনাগ্রহ নিয়ে তারা এখন আর অবাক হয় না।
সব দিক মিলিয়ে দেখা যায়, চীনের সামনে কোনো বিকল্প ছিল না—উইগুর সমাজে অনুপ্রবেশ করা সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করাই ছিল একমাত্র পথ।
কাজটা কার্যকরভাবে করতে প্রয়োজন হয়েছিল দুই দিকের পদক্ষেপ—একদিকে কঠোর ব্যবস্থা, অন্যদিকে ইতিবাচক প্রণোদনা। সহজভাবে বললে, একদিকে লাঠি, অন্যদিকে গাজর (ক্যারট অ্যান্ড স্টিক)। এখানে লাঠি বলতে স্পষ্টতই গ্রেপ্তার, অভিযান, নজরদারি, কারাবাস ও পুনঃশিক্ষা—এসব পদক্ষেপকে বোঝানো হয়েছে। এসব সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশেও দেখা যায়, যেখানে সন্ত্রাসের হুমকি তুলনামূলক কম।
সফরের সময় এই অংশ নিয়ে কেউই খুব একটা কথা বলতে চায়নি, কারণ বিষয়টি স্পর্শকাতর। তবে বাস্তবতা হলো, শেষ বড় সন্ত্রাসী হামলাটি ঘটেছিল ২০১৬ সালে। হুমকি একেবারে শেষও হয়নি।
চীনের নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা জানালেন, তাদের বিশ্বাস—সিনচিয়াং এখন নিয়ন্ত্রণে আছে। কারণ সরকার এখন গ্রামীণ উইগুর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করতে এবং তাদের সংস্কৃতি, ভাষা ও বিশেষভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি সম্মান জানাতে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। আর এটিই হলো সেই ‘গাজর’ এবং এটিই বেশি কার্যকর। সফরকালেও কাশগরে দেখা গেল উচ্ছ্বল, প্রাণবন্ত সংস্কৃতিগুলোর সহাবস্থান, যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে মেলামেশা করছে।
চীনের ধারণা হলো—যদি উইগুররা সমৃদ্ধ হয় এবং তাদের প্রতি যদি সম্মান দেখানো হয়, তবে তাদের উগ্রপন্থার পথে কেউ টেনে নেবে, এমন সুযোগ কম। ভয়টা হলো—যদি মানুষ দারিদ্র্যে ডুবে থাকে, তবে বাইরের শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলো টাকার লোভে ব্যবহার করে অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। এখন তাই চীনের শহর ও গ্রামের জীবনমানের পার্থক্য কমাতে বড় প্রকল্প চলছে। অগ্রগতি হচ্ছে। তবে কর্মকর্তারা বলছেন—এখনও অনেক বাকি।
সরকারি কোনো ব্রিফিংয়ে না থাকলেও, স্থানীয় অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন—যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া কিংবা এমনকি ইসরায়েলের মোসাদের পক্ষ থেকে সিনচিয়াংয়ে সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে। জানা গেছে, ইস্ট তুর্কিস্তান ইন্ডিপেনডেন্স মুভমেন্ট (ইটিআইএম), আইএস–খোরাসান এবং অন্যান্য জঙ্গিগোষ্ঠী এখনো সক্রিয়। প্রতিবেশী দেশগুলোয় তাদের উপস্থিতি বাড়ছে, যদিও তারা কোথা থেকে সমর্থন পাচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়।
আফগানিস্তান ইতোমধ্যে চীনের জন্য বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর—অর্থাৎ পশ্চিমা দেশগুলোর সরে যাওয়ার পর চীনের আশঙ্কা বেড়েছে যে, সেখানে থাকা উগ্রবাদের প্রভাব সিনচিয়াংয়েও ছড়াতে পারে। এ কারণে চীন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াখান করিডোরে সীমান্ত নজরদারি ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে। এ কাজে সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর ছোট ড্রোনও ব্যবহার করা হচ্ছে।
আফগানিস্তান নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ মনে করেন, তালেবান দেশটির অর্থনীতি ঘুরিয়ে দাঁড়াতে চায় এবং চীনের অর্থায়নে নতুন রেলপথ গড়ে উঠলে তারা ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ প্রকল্পে সহযোগিতা করবে। তবে অধিকাংশ বিশ্লেষক আশাবাদী নন। তাদের মতে, কাবুল সরকার বহু প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করতে না পারায় দেশটি চরমপন্থার উর্বর ভূমি হয়েই থাকবে।
আরেক উদ্বেগের বিষয় হলো—সিরিয়ায় এখন প্রায় ২০ হাজার উইগুর আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যাদের মধ্যে প্রায় ৫ হাজার প্রশিক্ষিত যোদ্ধা এবং বাকিরা হলো ওদের পরিবার। ২০১৩ সালের দিকে তারা আল-কায়েদা ও ইটিআইএম–এর সঙ্গে থেকে সিরিয়ার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। এখন যুদ্ধ শেষ, তারা কার্যত দিকহীন। আরও কিছু যোদ্ধা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানেও ছড়িয়ে আছে বলে ধারণা।
চীনের ভয়—এরা একসময় সিনচিয়াংয়ে ফিরে এসে সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। এই আশঙ্কা কেবল চীনের নয়; অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ অনেক দেশই মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে আসা প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের নিয়ে একই উদ্বেগে ভুগছে।
এতেই বোঝা যায়, কেন চীন ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগ্রহী। তাদের হিসাবটা হলো, যদি এসব দেশ সমৃদ্ধ হয় (যেমন সিনচিয়াংয়ের উন্নতি হচ্ছে), তবে ইসলামি উগ্রবাদের বিস্তার রোধ করা সহজ হবে। এই কারণেই সম্ভবত ইটিআইএম বারবার গ্যাস পাইপলাইনসহ বিআরআই অবকাঠামোয় হামলার হুমকি দিচ্ছে—যা চীন খুব গুরুত্বসহকারে নিচ্ছে।
চীন উইগুরদের জীবনমান উন্নত করতে দীর্ঘমেয়াদি ও সুসংগঠিত উদ্যোগ নিচ্ছে, যা অর্থনৈতিকভাবে বিআরআই–এর লক্ষ্যগুলোর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেউ কেউ বলতে পারেন, এসব সাজানো। কিন্তু ৩০ জন সাংবাদিককে দিন-রাত শহরে অবাধে ঘোরাঘুরি করতে দিয়ে তাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে—এটি অলীক ধারণা।
পরিশেষে বলা যায়, উইগুর সংস্কৃতির ধ্বংসের কোনো আলামত লেখকের চোখে পড়েনি। বরং দেখা গেছে, উইগুর ও কাজাখদের মতো সংখ্যালঘুরা নিজেদের ভাষায় পত্রিকা, টেলিভিশন ও রেডিও চালাচ্ছে। তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় সরকার জাদুঘরসহ নানা পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের কাজ করছে। মানুষ তাদের ধর্মীয় অনুশীলনও করতে পারছে। শর্ত হলো, সেটা হতে হবে আইনসঙ্গত, যেমনটা অস্ট্রেলিয়াতেও হয়। উরুমছি সফরের সময় একটি ইমাম প্রশিক্ষণ কলেজে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে প্রায় এক হাজার তরুণ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধায় পড়ছে, হালাল খাবার খাচ্ছে ও পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরি সুবিধা পাচ্ছে।
যদি চীন সরকার সত্যিই কোনো ‘উইগুরবিরোধী’ নীতি নিত, তবে এমন প্রতিষ্ঠান টিকতোই না। এ ছাড়া ‘উইগুরদের দাসশ্রমে বাধ্য করা হচ্ছে’ এই দাবি চীন সরকার পরিচালিত কর্মসংস্থান কর্মসূচির বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না। এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য স্থানীয় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়ন। কর্মকর্তাদের মতে, অতিরিক্ত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিলে সেটি উল্টো উগ্রবাদকেই উসকে দিতে পারে—তাই এখানেও এখন ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছে তারা।
স্থানীয় অনেক উইগুর লেখককে অনুরোধ করেছেন, লেখক যেন অস্ট্রেলিয়ানদের বলেন, তারা যেন সিনচিয়াং ভ্রমণে আসেন। কারণ তারা আরও বেশি বিদেশি পর্যটক চান। অঞ্চলটি অতিথিপরায়ণ, নিরাপদ ও সংস্কৃতিতে ভরপুর।
সূত্র: সিএমজি বাংলা