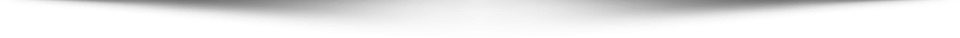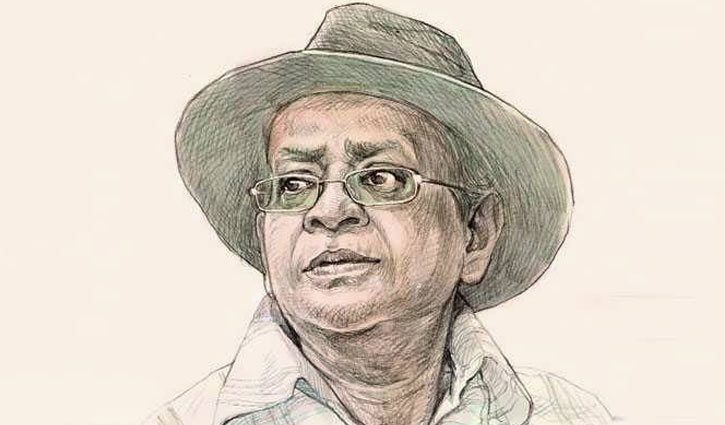
নন্দিত লেখক শাখাওয়াত হোসেনের ফেসবুক পোস্ট থেকে
হুমায়ূন আহমেদ ছোটগল্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আরেকটু স্পেসিফিক করি: হুমায়ূন আহমেদ হরর ছোটগল্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তার সময়কালীন ভালো হরর রাইটার খুঁজে পাওয়া মুশকিল; যদি পাওয়াও যায়, তবে হুমায়ূনের হররের ধারে কাছে কারোর আসার ক্ষমতা খুব একটা কারোর ছিল বলে মনে হয় না।
হুমায়ূনের হররের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক হররের তুলনা দিতে পারি আমি নির্দ্বিধায়। হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যের মডার্ণ হররের কর্ণধার। তার বেশ ভালো সংখ্যক হরর ছোটগল্প আছে। আমি আমার ব্যক্তিগত পছন্দের হরর হিসেবে নিই, বীণার অসুখ, দ্বিতীয়জন কিংবা সে। দেবী ও নিশীথিনী বাদ দিয়েও মিসির আলির ‘আমি ও আমরা’ আলাদাভাবে নজরকাড়ে তার ভয়াবহ হরর এলিমেন্টগুলোর কারণে।
উপরোক্ত ছয়টা হরর গল্পে আমরা হরর হিসেবে কী পাচ্ছি? এই প্রশ্নটার উত্তরের সাথেই জড়িত, কেন হুমায়ূন আহমেদ হরর গল্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বীণার অসুখের হরর হচ্ছে, একটা মানুষ তাকে ফলো করছে, তার কোনো ক্ষতি করছে না, কিন্তু কেন ফলো করছে সে জানে না। দ্বিতীয়জনের হরর হচ্ছে, একটা মানুষকে দুই জায়গায় সে দেখতে পাচ্ছে, ওই মানুষটা তার কোনো ক্ষতি করছে না। ‘সে’ গল্পের হরর হচ্ছে, একটা মেয়ে একটা অদ্ভুত প্রাণী জন্ম দিয়েছে, যদিও প্রাণীটা কারোর ক্ষতি করছে না। দেবী গল্পের হরর হচ্ছে, কামরার বাইরে পায়ের শব্দ, গন্ধ। নিশীথিনীর হরর হচ্ছে, হাফপ্যান্ট পরে লোহার রড হাতে নগ্ন গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা যুবক। আমি ও আমরা’র হরর হচ্ছে এক যুবকের নিঃসঙ্গ জীবন।
স্টিফেন কিং হরর লেখেন খুবই চতুর একটা উপায় অবলম্বন করে। তার হররের সবচেয়ে ভয়াবহ অংশটা থাকে লুকোনো। যেমন ধরা যাক, দ্য মিস্ট। একটা রহস্যময় কুয়াশায় সারা এলাকা ঢেকে গেছে আর ওই কুয়াশার মধ্যে একদল মানুষ একটা শপিংমলে আটকা পড়ল। শপিংমলের বাইরে ঘুরে বেড়াতে লাগল অদ্ভুত সব প্রাণী, যারা মানুষ হত্যা করছে। এই প্রাণীগুলোই হলো স্টিফেন কিং-এর ডিসট্র্যাকশন। অথচ পুরোটা সময়জুড়ে হররটা শপিংমলের বাইরে নয়, অবস্থান করছিল শপিংমলের ভেতরে। ইভিল কখনোই বাইরে ছিল না, ছিল ভেতরে, নিজেদের আশপাশেই। যে মানুষগুলো আটকা পড়েছে শপিংমলের ভেতর, বাঁচার জন্য অথবা যার যার স্বার্থে যে যতটুকুন পৌঁছায়- ওই গন্তব্যটাই হচ্ছে দ্য মিস্টের হরর।
শুধু কিং নয়, ‘দ্য থিং’ নামে একটা টেরিফাইং হরর আছে, আমার খুব প্রিয়, ওই হররটাও এই সূত্র মেনে বানানো। এন্টার্কটিকার একটা জায়গায় হঠাৎ অজ্ঞাত কিছু একটা অ্যাটাক করে একদল রিসার্চারের উপর, যার সম্পর্কে ওরা কেউই সঠিক জানে না- ওটা ঠিক কী। শুধু জানে, ওই জিনিসটা যে কারোর ভেতর ঢুকে থাকতে পারে আর মানুষ মারতে পারে। দ্য থিং টেরিফাইং একটা হরর কারণ সে মানুষ দেদারসে মারছে বলে নয়, কারণ ওরা একদল মানুষ কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না আর- তাই। ডিসট্র্যাকশনের আড়ালেই লুকিয়ে আছে রিয়েল হরর।
হুমায়ূন আহমেদের হররে এই বিষয়টা প্রবল আকারে বিদ্যমান ছিল। হুমায়ূন আহমেদের সবচেয়ে টেরিফাইং ভয়ের গল্প কোনটা জিজ্ঞেস করলে একগাদা গল্পের নাম আসবে। আমি একটা অসম্ভব সুন্দর গল্প নিয়ে গল্প করি আজ। এই গল্পটা ভয়ানক আন্ডাররেটেড। গল্পটা ভয়ের, গল্পের নামও ভয় এবং এই গল্পে কোনো ভুত নেই। এই গল্পে আছে শুধু আবহ। এই ভৌতিক থমথমে গা শিউরে উঠা আবহ কিভাবে তৈরী করেছেন হুমায়ূন? ভয় গল্পটার ভয় কোথায়?
একজন ব্যক্তি যার কোনো নাম দেওয়া হয়নি, ধরি তার নাম এক্স; এক্স ভদ্রলোক একটা অজপাড়া গাঁয়ে গিয়েছেন কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার এগজামিনার হয়ে। তার থাকার জায়গা হয়েছে কেমিস্ট্রি ল্যাবের পাশের একটা কামরায়, যেটা আগে স্টোররুম ছিল বলেই ধারণা তার। পুরো কামরায় একটা খুবই ছোট্ট জানালা। আর কলেজটাও একটা পরিত্যক্ত রাজবাড়ি। চারপাশে জঙ্গল। পরীক্ষার কারণে পুরো কলেজ ফাঁকা, কোনো লোকজন নেই।
অজপাড়া গাঁ, জঙ্গলের মাঝখানে একটা পরিত্যক্ত রাজবাড়ি, একটা কামরা যার জানালা খুবই ছোট্ট; তিনটা ইনফরমেশন ‘ভয়’ গল্পের একদম প্রথম প্যারায় পাওয়া যাচ্ছে। যেহেতু গল্পটা উত্তম পুরুষে বলা, ফলে পাঠককে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে ঠিক ওই জায়গায়, ওই সময়ে, ওই অবস্থায়। এক্স ভদ্রলোক কি একদমই একা ওখানে? না, তার সঙ্গে আছেন কালিপদ নামে এক দারোয়ান। সন্ধ্যার সময় হারিস নামে একজন লোক হারিকেন হাতে নিয়ে এসে চতুর্থ ইনফরমেশন দেয় তাকে। তা হলো- রাত দশটার আগে বিদ্যুত থাকে না। বিদ্যুত আসে দশটার পর।
পাঠক হিসেবে যখন আমি সন্ধ্যাবেলায় অজপাড়া গাঁয়ে জঙ্গলের মাঝখানে একটা পরিত্যক্ত রাজবাড়ির কোনো এক কামরায় হারিকেনের আলোয় বসে আছি, তখন গল্পে প্রবেশ করে সিরাজ উদ্দিন। সিরাজ উদ্দিন বেঁটেখাটো একজন মানুষ, মুখভর্তি চাপদাড়ি, মাথায় টুপি, চোখে সুরমা, গায়ে আতরের গন্ধ, চমৎকার স্বাস্থ্য তার। আর এটাই তার সাথে প্রথম দেখা নয়, সকালবেলাও সিরাজের সাথে এক্স ভদ্রলোকের দেখা হয়েছে। সিরাজ এতটাই সাধারণ একজন মানুষ যে, তাকে আলাদা করে কিছু মনে হয়নি তার।
‘ভয়’ গল্পের সবচেয়ে টেরিফাইং চরিত্রটাকে এক্স ভদ্রলোক প্রথমবারের সাক্ষাতে আবিষ্কারও করতে পারেননি তিনি এই গল্পের প্রধান চরিত্র। কলেজে এক্স ভদ্রলোককে সাহায্য করবেন সিরাজ, তাই দেখা সাক্ষাত, আলাপ আলোচনা হওয়া জরুরি। সিরাজ উদ্দিন সন্ধ্যাবেলায় একলা ভদ্রলোকের বাসায় এসে শুরু করলেন সাপ নিয়ে গল্প বলা। জানা গেল, কলেজের আশপাশ প্রচুর সাপ। সিরাজ বারংবার সতর্ক করেন, এক্স ভদ্রলোক যেন প্রতিবার কামরা থেকে বের হওয়ার সময় শব্দ করে বের হন। রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত সিরাজ উদ্দিন সাপের গল্প করেন এক্স ভদ্রলোকের সাথে। আর তার মাথায় খুব ভালোমতোন ঢুকিয়ে দেন, বাইরে সাপ আছে।
এতক্ষণ অবধি পাঠক হিসেবে আমি বুঝতে পারি না, সিরাজ উদ্দিনের উদ্দেশ্য কী? সাপের গল্প বলে ভয় পাইয়ে দেওয়া? যেখানে ভদ্রলোক বিরক্ত হচ্ছেন গল্প শুনতে, তাও জোর করে কেন বসে আছেন তিনি? কারণ আছে। প্রিন্সিপাল সাহেব এক্স ভদ্রলোকের জন্য খাবার পাঠাচ্ছেন। যাতে তাকে একা খেতে না হয়, সেজন্য সিরাজ উদ্দিনকে পাঠিয়েছেন প্রিন্সিপাল সাহেব নিজেই।
ওই খাবার আসতে দেরী হচ্ছে কারণ প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসায় ঝামেলা। এই ঝামেলাটা হলো, প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের মাথায় একটু সমস্যা আছে। ছেলেটা পাগল। আজ বটি দিয়ে মাকে কোপাতে গিয়েছিল, তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। এই ইনফরমেশনটাও সিরাজ উদ্দিন বেশ যত্ন করে দেন এক্স ভদ্রলোককে, কয়েক ধাপে। রাত সাড়ে দশটায় খাবার আসে, সিরাজ উদ্দিন খাবার খাওয়ার পরও রাত এগারটা পর্যন্ত বসে আরও কিছু সাপের গল্প করেন। আরও একবার ‘কামরার বাইরে সাপ’ মাথায় ঢুকিয়ে তারপর বিদায় নেন তিনি।
এই হলো ‘ভয়’ গল্পের প্রাথমিক সেটাপ। এখন, পাঠক হিসেবে গল্পের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। একটা জংলা জায়গা, একটা পরিত্যক্ত রাজবাড়ি, আশপাশ কেউ নেই, রাত এগারটা, একটা কামরার ভেতর আপনি, বিদ্যুত নেই, কামরায় হারিকেনের আলো, আপনি সুটকেস খুলে বই বের করে পড়ার বন্দোবস্ত করছেন আর আপনার হঠাৎ করেই মনে হলো, দরজার ওপাশে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। দরজার ওপাশ আপনি দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে, অশরীরি কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে দরজায় আর সে আপনার ক্ষতি করতে পারে। লজিক্যাল কোনো ব্যাখ্যা নাই এই ভয়ের কিন্তু প্রচণ্ড ভয়ে আপনার শরীর থরথর করে কাঁপছে। আপনি অজান্তেই চেঁচালেন- কে? আর তখন দরজা থেকে একটা পায়ের আওয়াজ থপ থপ করে চলে গেল দূরে। ভয়টা আচমকা কেটে গেল।
এটাই হলো ‘ভয়’ গল্পের এক্স ভদ্রলোকের এক্সপেরিয়েন্স করা ভয়। খুবই ছোট্ট মুহূর্ত, খুবই ক্ষুদ্র কিন্তু তীক্ষ্ণ তীব্র অনুভুতি। এই অতি স্বল্প মুহূর্তের ভয়ের কোনো অর্থ নেই। তিনি কখনো কাউকে দেখেননি। শুধু অনুভব করেছেন দরজার ওপাশে কারোর উপস্থিতি। পুরো গল্পজুড়ে এই ভয়টা এক্স ভদ্রলোক আরও দু’বার পান।
তিনি দ্বিতীয়বার ভয় পান যখন পরদিন রাত নয়টার দিকে সিরাজ উদ্দিন আসেন তার কামরায়। তবে ওই রাতে তিনি সাপের গল্প করেননি। তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে বিদায় নেন। সিরাজ উদ্দিন বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক্স ভদ্রলোক প্রচণ্ড ভয় পান। এতটাই বেশী যে একপর্যায়ে তার মনে হলো, তিনি জ্ঞান হারাবেন। তার শুধু মনে হলো, দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে, নক দিতে গিয়েও দিচ্ছে না। তারপর ভয়টা আচমকা কেটে গেল আবার।
দ্বিতীয়বার ভয় পাওয়ার সাথে আরেকটা বিষয় পরিষ্কার হয়, সিরাজ উদ্দিনের গল্প শুনলেই শুধু ভয় পাচ্ছেন এক্স ভদ্রলোক, তা নয়। যে রাতে সিরাজ উদ্দিন গল্প বলেননি, সেই রাতেই ভয় পাচ্ছেন তিনি। এবং দুইবারই ভয় পেয়ে এক্স ভদ্রলোক কামরা থেকে বের হয়েছেন। বাইরে ফকফকা জোছনা দেখেছেন, নির্জন জঙ্গল তাকে ভীত করেনি তখন। তিনি বাস্তব জীবনে যথেষ্ট যুক্তিবাদী মানুষ। ভুতপ্রেতে বিশ্বাস নেই। বিজ্ঞান পড়েছেন, লজিকে বিশ্বাস রাখেন। ফলে এই ব্যাখ্যাতীত আচমকা ভয় তাকে বেশ কিছু প্রশ্নের মুখে ফেলল। আর অচিরেই তিনি আবিষ্কার করলেন ‘ভয়’ গল্পের সবচেয়ে টেরিফাইং অংশটা। ওই অংশ হলো- এই ভয়টা তিনি পাচ্ছেন যখন সিরাজ উদ্দিন তার কাছে আসছে আর বিদায় নিচ্ছে শুধু তখন।
সিরাজ উদ্দিন কি ভুতপ্রেত বিশ্বাস করেন? না। সিরাজ উদ্দিন বিশ্বাস করেন, গ্রামের মানুষ বিভিন্ন কুসংস্কারে বিশ্বাস রাখে, ওসব বাকোয়াস। তবে সিরাজ উদ্দিন বিশ্বাস করেন জ্বিন। এই তথ্য আমরা জানতে পারি, যখন দ্বিতীয়বার ভয় পাওয়ার পর জেদী ও বুদ্ধিমান এক্স ভদ্রলোক দারোয়ান কালিপদকে সঙ্গে নিয়ে সিরাজ উদ্দিনের বাসায় চলে যান, ওই রাতেই, ওই সময়। তিনি জানতে চান, তার ভয়ের উৎস, তিনি বুঝতে চান ভয়ের সাথে সিরাজ উদ্দিনের সম্পর্ক কী!
একটা টিপিক্যাল এন্টাগোনিস্ট, যার কাজ ভয় দেখানো- সে কী করবে যখন জানতে পারবে তার টার্গেট করা লোকটা ভয় পাচ্ছে। স্বাভাবিকতই তাকে আরও ভয় দেখাবে। নিজের চতুরতা জাহির করবে। এন্টাগোনিস্ট মাত্রই নিজের বুদ্ধিমত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা নিয়ে অবসেসড থাকে। ‘ভয়’ গল্পের সিরাজ উদ্দিনের ওই অবসেসন নাই। নাই বলেই এই সিরাজ উদ্দিন একটা আনপ্রেডিক্টেবল ভয়ের জন্ম দিচ্ছে পুরো গল্পজুড়ে। কারণ, আমরা সিরাজ উদ্দিনকে আর কাল্পনিক অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী কেউ বলে কল্পনা করতে পারছি না। তাকে খুবই সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে নিতে হচ্ছে আমাদের, যার সাথে প্রথমবার দেখা হলে তাকে মনে রাখার কোনো বিশেষ কারণও থাকে না।
যখন এক্স ভদ্রলোক কালিপদকে সঙ্গে নিয়ে রাত্তিরে তার বাসায় যান, সিরাজ উদ্দিন তাকে বেশ আদর যত্ন করে খাওয়ান। সিরাজ উদ্দিন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তখন। তিনি একা থাকেন, বিয়েশাদী করেননি, একসময় আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল, এখন তার অল্প-স্বল্প ধানি জমি হয়েছে। তিনি একা, বিয়ে করেননি, একসময় দরিদ্র ছিলেন- এই তিনটা ইনফরমেশন খুবই জরুরি। আর এই ইনফরমেশন অবধি এসে আমরা হুমায়ূন আহমেদের আরেকটা ভৌতিক আর্টপিসকে রেফারেন্স হিসেবে নিয়ে আসতে পারি। ওই আর্টপিসের নাম, বৃহন্নলা। সুধাকান্ত বাবুর সঙ্গে কি আমরা সিরাজ উদ্দিনের মিল পাচ্ছি?
হ্যাঁ, দুইজনই একা থাকেন, দুইজনই বিয়েশাদী করেননি এবং দুইজনের সাথেই শিক্ষকতার বিষয় জড়িত। কিন্তু বৃহন্নলা হরর গল্প হয়েও আদতে হরর নয়। হুমায়ূন আহমেদ বৃহন্নলা শেষ করেছেন স্টিফেন কিং-এর পথ অবলম্বন করেই। দেয়ার ইজ নাথিং মোর ইভিল দ্যান হিউম্যানস। কিন্তু ‘ভয়’ গল্পটা শেষ হয়নি ওভাবে। দু’টো গল্প পড়তে গেলে আমার মনে হয়, হুমায়ূন আহমেদ বৃহন্নলায় টুইস্ট দিতে যেয়ে যে হররটা মিস করেছেন, ওই হররটা ‘ভয়’ দিয়ে পূর্ণ করেছেন। ভয় হয়ে উঠেছে হিউম্যান সাইকোলজির মিশ্রণে পুরোদস্তুর হরর।
গল্পে ফিরি… এক্স ভদ্রলোক তৃতীয়বার ভয় পান, রাতে বাড়ি আসার পর সিরাজ উদ্দিন যখন তাকে বিদায় দিতে এগিয়ে আসেন বাড়ির কাছে বিরুই নদী পর্যন্ত। ফকফকা জোছনায় যখন জোর করে কালিপদের হাতে একটা হারিকেন ধরিয়ে সিরাজ উদ্দিন বিদায় নেন, তখন এক্স ভদ্রলোক তাকিয়ে থাকেন তার যাওয়ার দিকে। তিনি আসলে পরীক্ষা করতে চান, ঠিক কোন সময় থেকে এবং কিভাবে ভয়টা তিনি পান। যখন বাঁশঝাড়ের আড়ালে সিরাজ উদ্দিন হারিয়ে যান, ঠিক তখনই এক্স ভদ্রলোক তৃতীয়বারের মতোন মুখোমুখি হন ওই ভয়ের। তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু তার মনে হচ্ছে, একটা অশরীরি অশুভ কিছু তার দিকে ছুটে আসছে ওদিক থেকে এবং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওটা। যে ভয়টা তিনি পাচ্ছেন, ওই ভয়টা এই জগতের নয়। এক্স ভদ্রলোক হুমড়ি খেয়ে পড়েন আর ঠিক তখনই ভয়টা চলে যায় তার।
আমরা ‘ভয়’ গল্পটাকে যদি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলি, তবে সমস্ত টুকরো জড়ো দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি- সিরাজ উদ্দিনের সঙ্গে অশরীরি কেউ থাকে। আর এখানেই ‘ভয়’ গল্পটা আপনাকে সামান্য অস্বস্তিতে ফেলে। অশরীরি সাধারণত পরিবেশ চেপে ধরে, আশপাশকে জানান দেয় তার উপস্থিতি। ধরা যাক, বন্ধুদের আড্ডায় যদি অশরীরি উপস্থিত হয়, তবে প্রতিটা বন্ধুই তা অনুভব করবে। প্ল্যানচেটে জ্বালানো মোমবাতি নিভে গেলে অন্ধকার পুরো কামরায় ছড়িয়ে পড়ে, খণ্ড খণ্ড হয়ে নয়।
সিরাজ উদ্দিনের সঙ্গে যদি অশরীরি থাকে, তবে ওই অশরীরি নিজের উপস্থিতি সবাইকে জানান দেবে। যদি ভয়ের কিছু থাকে, তবে নিকটে দাঁড়িয়ে থাকা কালিপদও ভয় পাবে। কিন্তু কালিপদ ভয় পায়নি। তার কাছে কিছুই মনে হয়নি। অর্থাৎ, ভয় নিয়ে যা চলছে, তা শুধুই এক্স ভদ্রলোকের মাথার ভেতর। একটা বৃত্ত কেন্দ্র করে এই ভয়টার উৎপাদন হচ্ছে যে বৃত্তে আছে শুধু এক্স ভদ্রলোক। এই ভয়টা আদতে পরিবেশ না, এই ভয়ের উৎস নিতান্তই তার নিজের ভেতর। আর এইখানে এসে ‘ভয়’ গল্পটা মোড় নেয় পুরোদস্তুর সাইকোলজিক্যাল গন্তব্যে।
তৃতীয়বার ভয় পাওয়ার পর এক্স ভদ্রলোক অজপাড়া গাঁ ছেড়ে চলে আসেন, তার কাজ বাকি রেখেই। তিনি কেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? কারণ, তিনি জানতে পেরেছেন প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলেটার অসুস্থতার পেছনেও সিরাজ উদ্দিনের হাত আছে। ওই ছেলেটা সদ্য বিয়ে করেছিল, বেড়াতে এসেছিল গ্রামে, সাত দিনের ছুটি নিয়ে। রাতে সিরাজ উদ্দিন আসলেন, তার সাথে সাপের গল্প করলেন, বিদায় নেওয়ার পর হঠাৎ করেই ছেলেটা প্রচণ্ড ভয় পেল, ভয়ে মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়ে গেল তার। কিছুক্ষণ পরই ছেলে আবার ঠিকঠাক। কিন্তু কিছুদিন পর আবার ভয় পেল সে। সেদিনও সিরাজ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। তারপর থেকে রোজ রোজ ভয় পেতে লাগল। কোনো চিকিৎসায় কাজ করল না। এখন পুরোপুরি পাগল। দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয় তাকে।
প্রিন্সিপাল সাহেব আরেকটা অস্বস্তিকর ইনফরমেশন দেন তাকে। সেটা হলো- একমাত্র সিরাজ উদ্দিন বাসায় আসলেই তার পাগল ছেলেটা শান্ত থাকে। মুচকি মুচকি হাসে তখন। সিরাজ উদ্দিন তার গায়ে ও মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। যেহেতু প্রিন্সিপাল সাহেবের ছোট বাচ্চাকে টিউশনি পড়ান সিরাজ উদ্দিন, ফলে প্রতিদিন যেতে হয় তাকে ওই বাড়িতে। এবং কখনো ওই টিউশনি মিস দেননি তিনি। কিন্ত কিছু দিন ধরে সিরাজ উদ্দিন বাসায় কম আসছেন, এক্স ভদ্রলোককে সময় দিচ্ছেন, তাই ছেলেটা উগ্র হয়ে গেছে, বটি দিয়ে মাকে কোপাতে গেছে সেদিন। প্রিন্সিপাল সাহেবের মুখে এই গল্প শুনে অজানা ভয়ে ট্রমাটাইজড হয়ে এক্স ভদ্রলোক তার পাগল ছেলেটাকে একবার দেখতে চান। দড়ি দিয়ে বাঁধা, মুখ দিয়ে লালা পড়ছে, পশুর মতো গোঙাচ্ছে ছেলেটা। দেখার পর এক্স ভদ্রলোক ওই রাতেই গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন।
‘ভয়’ গল্পটা শেষ হচ্ছে চার বছর পর সিরাজ উদ্দিনের সাথে পুনরায় একবার এক্স ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ দিয়ে। বায়তুল মোকারমের ফুটপাতে তাদের সাক্ষাৎ হলো। আর হাসিমুখে সিরাজ উদ্দিন জানালেন, এক্স ভদ্রলোকের কথা তার মনে পড়ে। আর সঙ্গে এও জানান, প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলেটার লাশ পাওয়া গিয়েছিল পরে। তিন দিন ধরে উধাও থাকার পর বাড়ির পাশের নদীর ঘাটে লাশটা পান সিরাজ উদ্দিন নিজেই। এবং সর্বশেষ ইনফরমেশন দেন সিরাজ উদ্দিন। ছেলের মৃত্যুর পর প্রিন্সিপাল সাহেব জামালপুর চলে যান আর নতুন প্রিন্সিপাল যিনি আসেন পরিবার সহ, কিছুদিন ধরে তার সঙ্গেও বেশ গল্পগুজব হচ্ছে তার। সমস্যা হলো, প্রিন্সিপাল সাহেবের স্ত্রী মাঝে মাঝে বিনা কারণে ভয় পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করেন। সিরাজ উদ্দিনের ধারণা, বাড়িটারই বোধহয় দোষ।
এক্স ভদ্রলোক কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকেন সিরাজ উদ্দিনের দিকে। সিরাজ উদ্দিনের মুখে সরল হাসি, চোখজোড়া মমতামাখা। গল্পটা শেষ আর শেষের এই অংশে এক্স ভদ্রলোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি যা অনুভব করবেন- তা হলো এই গল্পের মূল ভয়।
আপনি জানেন, সিরাজ উদ্দিন সাধারণ মানুষ নয়। কিন্তু আদতে সিরাজ উদ্দিনের মধ্যে বিশেষত্ব নেই কোনো, তিনি সাধারণই। আপনি জানেন, সিরাজ উদ্দিন বিদায় নিলে প্রচণ্ড ভয়ে আপনি আবার আচ্ছন্ন হবেন, যে ভয়ের কোনো লজিক নেই। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন না, এমন কিছু জগতে হয় এবং আপনি জানেনও না, এই ভয় থেকে আপনি কিভাবে বাঁচবেন। আপনি জানেন, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা একটা ভয়ানক সিরিয়াল কিলার, যদিও তার খুন করার ধরণ খুবই রেয়ার, কিন্তু আপনি কিছু করতে পারছেন না, কারণ আপনার হাতে কোনো প্রমাণ নেই। আপনার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।
একটা পুরোদস্তুর হতাশ, অসহায়, ভীত, ক্ষোভ ও প্রচণ্ড রাগে জর্জরিত মানুষ হয়ে আপনি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন, সিরাজ উদ্দিন হাসছে, তার হাসিতে শিশুর সারল্য, চোখজোড়া মমতায় আর্দ্র। প্রথমবার ‘ভয়’ শেষ করে এই ক’টি লাইন আমি কয়েকবার পড়েছি। যেহেতু নিজে লিখি, একটা পারফেক্ট হরর গল্প শেষ কিভাবে হয়, জানার-শেখার ইচ্ছা আমার খুব। আর ‘ভয়’ গল্পটা শেষ হচ্ছে পারফেক্ট জায়গায়, পর্যাপ্ত, প্রোপার আর প্রচণ্ড ভয়াবহ একটা ভয়ের রেশ রেখেই। ওই ভয়টা হলো, সিরাজ উদ্দিনের হাসি, তার সহজ সরল চোখ।
‘ভয়’ গল্প পড়ার অনেক বছর পর কুরোসাওয়ার ‘কিউর’ সিনেমাটা দেখা হয় আমার। আর আমি পরিচিত হই ফিকশন জগতে আমার পড়া ও দেখা মোস্ট টেরিফাইং এন্টাগোনিস্টের সাথে, যার নাম মামিয়া। কিউর সিনেমার গল্প হচ্ছে, টোকিও শহরে হঠাৎ করে খুন বেড়ে গেছে। আর খুনগুলো কোনো সিরিয়াল কিলার করছে না, কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি করছে না, করছে আপনজন, আশপাশের মানুষ, প্রতিবেশী অথবা বন্ধু। এবং প্রতিটা খুনেই ভিক্টিমের শরীরে আঁকা হচ্ছে একটা ‘এক্স’ চিহ্ন।
প্রতিটা খুন আনপ্রেডিক্টেবল ও ব্যাখ্যাতীত।
যেমন ধরা যাক, সিনেমায় দেখানো প্রথম খুন (আগেও চার পাঁচটা হয়েছে)- প্রস্টিটিউট খুন হলো, খুনী পালিয়ে গেল না, ওখানেই লুকিয়ে রইল এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করল। দ্বিতীয় খুন, একটা কিউট কাপল। হঠাৎ করেই স্ত্রীকে মেরে ফেলল স্বামী, অপরাধও স্বীকার করল। তৃতীয় খুন, পুলিশ বুথ। এক পুলিশ তার সঙ্গের পুলিশের মাথায় গুলি করল। চতুর্থ খুন, ডাক্তার। প্রতিটা খুনের খুনীই নিজের অপরাধ স্বীকার করল কিন্তু যা করতে পারল না, তা হলো খুনের মোটিভ বের করা। কেন একজন স্বামী হঠাৎ স্ত্রীকে মেরে ফেলবে? কেন একটা পুলিশ, যার সঙ্গে এত বছর ধরে ডিউটি করছে, তাকে মেরে ফেলবে?
কিউর সিনেমার সাথে ‘ভয়’ গল্পের সংযোগ হচ্ছে এন্টাগোনিস্ট দিয়ে। কিউর সিনেমার প্রতিটা খুন, যদিও খুনী আলাদা কিন্তু সবাই আঁকছে একটাই কমন চিহ্ন- এক্স। অর্থাৎ, প্রতিটা খুনেই একটা কমন কিলার আছে। ওই কিলারটা হলো মামিয়া। পুলিশ যখন তদন্ত করে, তখন খুঁজে পায়, প্রতিটা খুনেরই খুনীর সঙ্গে খুন করার আগে কখনো না কখনো মামিয়ার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। ওই সাক্ষাৎ বড্ড ধোঁয়াশে। কারণ, মামিয়া এমনেশিয়ার রোগী। সে নিজের পরিচয় ভুলে গেছে, কোথায় থাকে জানে না, কোথা থেকে এসেছে জানে না। সে শুধু কথা বলে। সে শুধু প্রশ্ন করে। সে প্রতিটা মানুষকে প্রশ্ন করে। তার কমন প্রশ্ন- আমি কে? আমি কোথায় থাকি? তুমি কে? আর এইসব প্রশ্ন করতে করতে একটা সময় পর সে সামনের ব্যক্তিকে হিপনোটাইজ করে ফেলে। তারপর ওই ব্যক্তির অস্তিত্বের গোড়া ধরে টান দেয়। আমি একটা ছোট্ট উদাহারণ দিচ্ছি।
মামিয়াকে ধরা হয়েছে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তাদের কথোপকথন:
পুলিশ: তুমি তোমার সম্পর্কে কিছু মনে করতে পারো?
মামিয়া: না।
পুলিশ: তুমি কি জানো কেন তোমাকে এখানে আনা হয়েছে?
মামিয়া: তুমি কে?
পুলিশ: আমি ফুজিয়েরা, হেডকোয়াটার্স থেকে; তুমি কি জানো তোমাকে এখানে কেন আনা হয়েছে?
মামিয়া: কী?
পুলিশ: প্রশ্ন কোরো না, উত্তর দাও।
মামিয়া: কী প্রশ্ন?
পুলিশ: তুমি কি জানো তোমার অপরাধের জন্য তোমার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে?
মামিয়া: (পাশের পুলিশকে) এটা কি তোমার বস?
পুলিশ: প্রশ্নের উত্তর দাও।
মামিয়া: তুমি কে?
পুলিশ: ফুজিয়েরা, হেডকোয়াটার্স।
মামিয়া: কে?
পুলিশ: (রেগে) তুমি কি নিজেকে বেশী স্মার্ট ভাবো?
মামিয়া: তুমি কে?
পুলিশ: (পাশের পুলিশকে) এই ছেলের সমস্যা কী?
মামিয়া: আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি, তুমি কে?
পুলিশ: (রেগে) আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।
মামিয়া: ঠিক আছে, আমি তোমায় আরেকবার জিজ্ঞেস করছি। আমি জানি তুমি ফুজিয়েরা, হেডকোয়াটার্স থেকে। কিন্তু তুমি কে?
পুলিশ: (একটু থতমত খেয়ে) তুমি কী বলতে চাও?
মামিয়া: আমি কী বলতে চাচ্ছি, তা তুমি ভাবো।
এইটুকুনই কথোপকথন। পুরো কথোপকথন পর্বে জাস্ট কয়েকবার ‘তুমি কে’ প্রশ্ন করে মামিয়া একটা স্বাভাবিক সুস্থ পুলিশের আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের গোড়া ধরে টান দিয়েছিল। পুরো সিনেমায় সে এই কাজটা করে সবার সাথে। কিউর সিনেমার মূল হররটা হচ্ছে- প্রতিটা মানুষই ইভিল। আর প্রতিটা মানুষেরই ভেতর বাস করছে মনস্টার, মার্ডারার, রেপিস্ট, প্রচণ্ড রাগে ক্ষোভে জর্জরিত অসুস্থ একটা পশু। আর প্রতিটা মানুষই তা ঢেকে রাখছে। কিন্তু যখনই মামিয়ার মতো কেউ তাদের অস্তিত্ব ধরে টান দিচ্ছে, ওদের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে তা, যা সম্পর্কে ওরা নিখজেরাও ওয়াকিবহাল ছিল না।
কিউর সিনেমার হরর কিন্তু ‘মার্ডার’ নয়, হরর হলো এই সত্য- যে কাপলকে আমরা হ্যাপি দেখছি, ওই কাপলের মধ্যে অনেক গভীরে থাকতে পারে চরম আনহ্যাপিনেস। যে পুলিশকে আমরা ঠিকঠাক দেখছি, তার অনেক গভীরে থাকতে পারে তারই সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাওয়া পুলিশের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা। যে ডাক্তারকে আমরা দৈনিক একশো রোগী পরীক্ষা করতে দেখছি, তার ভেতরই নিহিত আছে কাউকে ব্রুটালি হত্যা করার সুপ্ত ইচ্ছা। আমরা ভেতর থেকে যা, আমরা বাইরে যা- মামিয়া আমাদের জানাচ্ছে, আমরা দুটোর কেউই না আসলে, আমাদের ভেতরটা শূন্য হওয়া উচিত, যেমনটা তার নিজের। কারণ মানুষ যখন নিজের ভেতর থেকে সবকিছু বের করে ফেলতে পারে, তখন সে অন্যদের ভেতরটাও দেখতে পায়। প্রতিটা মানুষের যাত্রা কী? গন্তব্য কোথায়? সে কে? কিউর সিনেমাজুড়ে এই প্রশ্নগুলোই আপনাকে হান্ট করবে, করে যাবে এবং করতে থাকবে। আমি কোনো ডিপ্রেসড মানুষকে ‘কিউর’ দেখার সাজেশন দিই না।
কারণ, প্রতিটা মানুষই জীবনে কখনো না কখনো ডাউনের চরম পর্যায়ে গিয়ে ছোট্ট একটা ধাক্কার অপেক্ষায় থাকে। জোকারের মতে, যা গ্রাভিটির মতোই অনেকটা, প্রয়োজন পড়ে শুধু একটা ধাক্কার। জাস্ট অ্যা লিটল পুশ। আমি ভয় পাই কারণ এই পুশটা কিউর দিয়ে ফেলতে পারে। এই পুশ দিতে পারে ডিটাচমেন্ট। এই পুশ দিতে পারে কাফকার কোনো গল্প। এই পুশ দিতে পারে মামিয়া কিংবা সিরাজ উদ্দিন।
‘ভয়’ গল্পের কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই, কিন্তু সচেতন পাঠক মাত্রই ধরতে পারবেন, সিরাজ উদ্দিন ও মামিয়ার খুন করার পদ্ধতির মধ্যে বিস্তর মিল। সিরাজ উদ্দিনের ওই ক্ষমতা আছে, কারোর মাথায় প্রবেশ করার, হিপনোটিজম এপ্লাই করছেন তিনি। মামিয়া প্রয়োগ করেছিল প্রশ্ন। সিরাজ উদ্দিন প্রয়োগ করছেন সাপের গল্প। সাপের গল্প বলে তিনি সম্মুখের ব্যক্তির নিজের ভেতরে লুকায়িত ভয়াবহ কোনো ভয় সামনে টেনে আনছেন। যে কারণে প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলে ভয় পাচ্ছে, বাকিরা পাচ্ছে না। এক্স ভদ্রলোক ভয় পাচ্ছেন, কালিপদ পাচ্ছে না। সিরাজ উদ্দিন সচেতন মনে একগাদা মানুষের মধ্যে গল্প বলেও একজন ব্যক্তিকে আলাদা করে টার্গেট করতে পারছেন। তার ভেতরের ভয়টা বের করে আনছেন এবং তাকে পাগল করে দিচ্ছেন। প্রশ্ন হলো কেন করছেন তিনি?
আমি কিছু কারণ খুঁজে পাই, যা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি। প্রথম কারণ, সিরাজ উদ্দিন মানসিকভাবে অসুস্থ। শৈশবে হতদরিদ্র ছিলেন ফলে স্বাভাবিকতই পৃথিবীর রুক্ষ বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তার। যেহেতু সাধারণ বিশেষত্বহীন মানুষ তিনি, সেহেতু কখনো কারোর মনোযোগও আকর্ষণ করেননি। এখন তার একটা ক্ষমতা হয়েছে, যা ব্যবহার করছেন তিনি এবং উপভোগ করছেন। লক্ষ করুন, কোনো দরিদ্র মানুষ তার ভিক্টিম নয়। তিনি টার্গেট করছেন সমাজে মোটামুটি ভালো অবস্থান আছে, সম্মান আছে- ওদের। উদাহারণ, প্রিন্সিপালের ছেলে কিংবা এগজামিনার। কিন্তু কালিপদ কিংবা হারিস নয়। তিনি পূর্ণ মনোযোগ পাচ্ছেন, তার বাসায় যাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকেন প্রিন্সিপাল স্বয়ং, কারণ তার পুত্রের শান্ত থাকার জন্য তাকে প্রয়োজন। একা ও নিঃসঙ্গ একটা মানুষের জন্য এইটুকুন অনেককিছু।
একা ও নিঃসঙ্গতা আসার পর আমি দ্বিতীয় আরেকটা কারণও অনুমান করতে পারি। যার খুবই ছোট্ট একটা ইঙ্গিত গল্পে ছিল। ওটা হচ্ছে, প্রিন্সিপালের ছেলের গায়ে হাত বুলানো। ওই লাইনটা লেখা যেত- প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের মাথায় হাত বুলালে শান্ত থাকে ছেলে। বাক্যে মাথার পাশাপাশি ‘গা’ আসার পর আমার কেন জানি মনে হয়- সিরাজ উদ্দিনের কাজকর্মের পেছনে সেক্সুয়াল পার্ভার্টনেসও যুক্ত। আমার ধারণা, সিরাজ উদ্দিনের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টশন স্ট্রেইট নয়। তার বিয়ে না করা, এক্স ভদ্রলোকের সাথে সম্পর্ক আর ‘ভয়’ গল্পের এন্ডিং- যা আরেকটু পরিষ্কার করে আমার ধারণা।
প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের লাশ পাওয়া যায় তিন দিন পর। ওই ছেলের সাথে সিরাজ উদ্দিন কী করেছেন, তা উহ্য। ‘আপনার কথা মনে পড়ে’- বলে সিরাজ উদ্দিন চার বছর পর এক্স ভদ্রলোকের সাথে সাক্ষাতে যে ইঙ্গিত করেন, যদি সেক্সুয়াল প্রেফারেন্স থেকে ভাবি, তবে ওটাও আমার ধারণা আরও পোক্ত করে। কিন্তু প্রোপার উত্তর আমার জানা নাই।
‘কিউর’ সিনেমায় মামিয়া কেন করছে ওইসব, তারও ঠিকঠাক উত্তর নেই। ভয় আর লজিক- দুটো বিপরীতমুখি বিষয়। যে ভয়ে লজিক থাকে, ওটা ভয় নয়। আমাদের ভয় সৃষ্টিই হয় লজিকহীন অবস্থা থেকে। যে প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা দাঁড়াই, তা ব্যাখ্যাতীত ও উত্তরহীন বলেই আমরা মূলত ভয় পাই। আমরা ভয় পাই কারণ সিরাজ উদ্দিনদের কাজকর্মের উত্তর নেই কিন্তু কাজকর্ম এক্সিস্ট করছে। আমরা ভয় পাই, কারণ এক্স ভদ্রলোক যা অনুভব করছেন, তা আমরা যে কেউ অনুভব করতে পারি, যেকোনো সময়। কার ভেতর সিরাজউদ্দিন লুকিয়ে আছে, তা আমরা জানি না।
আমরা ভয় পাই এটা জেনে যে, প্রতিটা মানুষ একেকটা নিউক্লিয়ার নিয়ে ঘুরছে। কে কখন ব্লাস্ট হয়, জানা নাই তার নিজেরও। আমরা ভয় পাই এটা জেনে যে, আমরা সবাই আছি, এক্সিস্ট করছি, কিন্তু কেন করছি তা জানি না। আমাদের ভেতর ভয় আছে, অনেক ভয়, লুকোনো ভয়, ওইসব ভয়ের কোনো অর্থ নেই কিন্তু আমরা অনুভব করতে পারি, কখনো না কখনো। আমরা ভয় পাই কারণ আমরা জানি, মাঝে মাঝে আমাদের বন্ধ কামরার ওপাশে সিরাজ উদ্দিনরা উপস্থিত হতে পারেন। যাদের হাত রক্তাক্ত কিন্তু মুখচ্ছবি সরলতায় ভরপুর, চোখজোড়া মমতায় আর্দ্র।
হুমায়ূন আহমেদ ১৯৯৭ সালে ‘আমার প্রিয় ভৌতিক গল্প’ নামে একটা বই সম্পাদনা করেন। ওই বইয়ের জন্য তিনি দুই বাংলা মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশটা ক্লাসিক ভুতের গল্প বেছে নেন। রবীন্দ্রনাথের নিশীথে, তারাশঙ্করের ডাইনী, বিভূতিভূষণের মায়া, বনফুলের অবর্তমান সহ অনেকগুলো চমৎকার হররের জায়গা হয়েছে ওই বইয়ে। নিজের মাত্র দুটো গল্পই অন্তর্ভুক্ত করেছেন হুমায়ূন আহমেদ। ওই দুটোর একটা হচ্ছে এই ‘ভয়’।
‘আমার প্রিয় ভৌতিক গল্প’ বইয়ের প্রকাশকাল আর ‘কিউর’ সিনেমা রিলিজড ডেট একই বছর; ১৯৯৭। দুটো ভিন্ন দেশের দুই প্রান্তে বসে দুটো প্রতিভাধর মানুষ নির্মাণ করেছেন এমন দুটো আর্ট, যার কোর কনসেপ্টের সাথে আছে চমৎকার সংযোগ। বাংলা সাহিত্যের একটা স্মরণীয় সময়ে বসে হুমায়ূন আহমেদ বিশ্বমানের ছোটগল্প লিখেছিলেন- তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু ‘মেঘ বলেছে যাব যাব’ কিংবা ‘অপেক্ষা’ দিয়ে নয়, তার প্রতিভা বুঝতে হলে আমাদের বেশী করে ডুব দিতে হবে তার ছোটগল্পের ভেতর। তার একেকটা গল্প, একেকটা জগত উন্মোচন করে। ওইসব বিবিধ ধূসর জগত কাঁধে নিয়ে আমাদের চলার বাকি আছে আরও।
আজ জাদুকরের জন্মদিন। কৃতজ্ঞতা, হুমায়ূন আহমেদ; আপনি না জন্মালে আমার এই জগতে আসা হতো না আর।