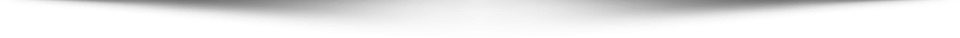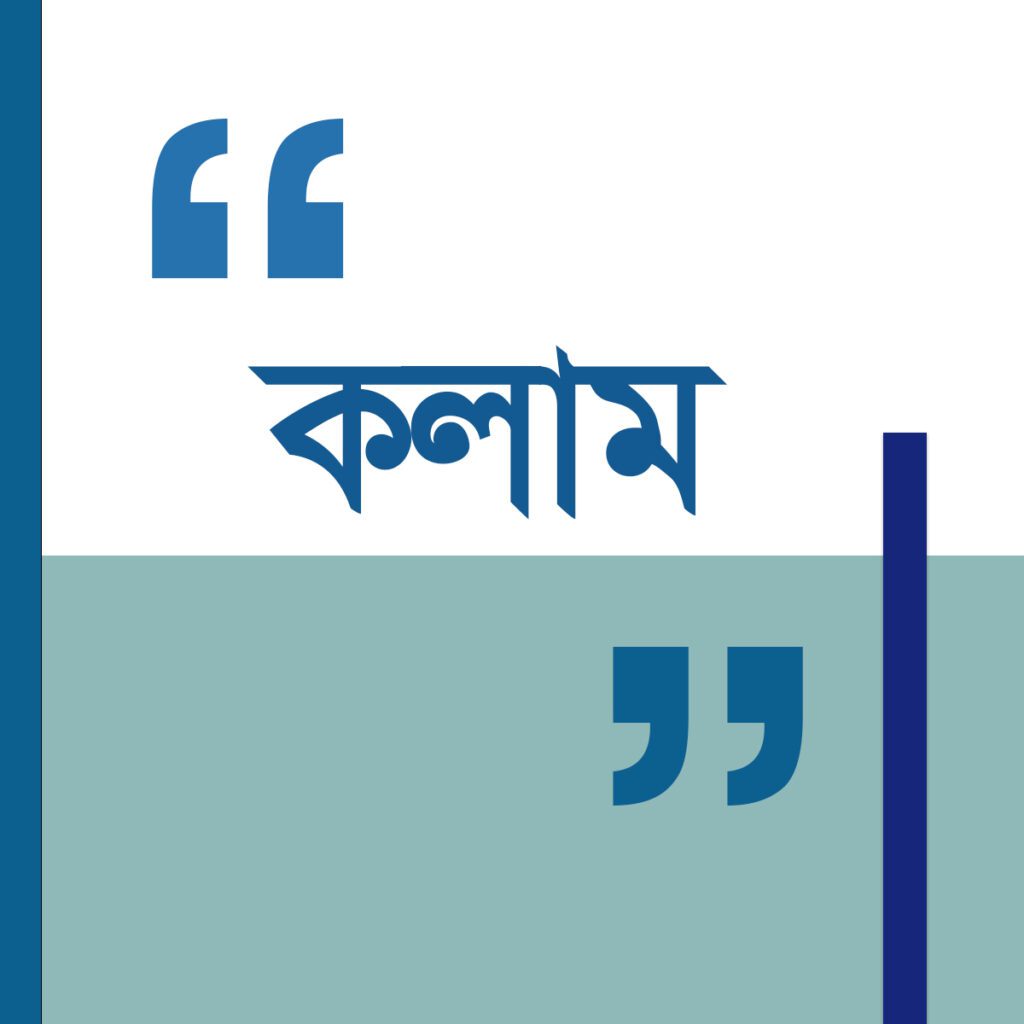
স্বপন বিশ্বাস
গণতন্ত্রকে বলা হয় শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপ। জনগণের ভোটাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সরকার পরিবর্তনের শান্তিপূর্ণ সুযোগ—এসবই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী যেভাবে রাজনৈতিক সংকট, জনঅসন্তোষ, দুর্নীতি, সামাজিক বিভাজন ও অস্থিতিশীলতা বাড়ছে, তাতে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন—গণতন্ত্র কি আর কার্যকরভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিরাপদ ব্যবস্থা? নাকি এটি এখন উল্টো ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠছে?
গণতন্ত্রের মৌলিক সমস্যা
গণতন্ত্র মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠতার শাসন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা সবসময় ন্যায্য কিংবা টেকসই নয়। অনেক সময় জনতার আবেগকে ব্যবহার করে নেতারা ক্ষমতায় আসেন, পরে তারা জনগণের স্বার্থ ভুলে গিয়ে কেবল ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার রাজনীতি করেন। ফলে দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব ও আইনের শাসনের অবক্ষয় অনিবার্য হয়ে ওঠে।
উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশে ভোটকে ঘিরে সহিংসতা, জালিয়াতি, অর্থ ও ক্ষমতার প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ফলে জনগণের আস্থা নষ্ট হচ্ছে। মানুষ বিশ্বাস হারাচ্ছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায়। একসময় ভোটাররা হয় উদাসীন হয়ে পড়ে, নয়তো প্রতিবাদে রাস্তায় নামে। এতে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ে, যা রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অচল করে দেয়।
বিশ্ব রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা
শুধু উন্নয়নশীল দেশ নয়, উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেও এই সংকট দৃশ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় থেকে গণতন্ত্রের গভীর বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্রেক্সিট গণভোট ব্রিটেনকে দীর্ঘ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় ফেলেছে। এমনকি ইউরোপীয় দেশগুলোতেও পপুলিস্ট নেতাদের উত্থান গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো “পপুলিজম” বা জনপ্রিয়তাবাদ। জনতার আবেগকে উসকে দিয়ে স্বল্পমেয়াদি জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিলেও তার দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অভিবাসী বিরোধী বক্তব্য বা ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি হয়তো তাৎক্ষণিক ভোটে জেতায়, কিন্তু রাষ্ট্রে গভীর সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করে।
অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় আঘাত
একটি রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা অপরিহার্য। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারগুলো প্রায়ই ভোটের রাজনীতির কারণে জনগণকে খুশি করার প্রকল্প হাতে নেয়—সাবসিডি, ভর্তুকি, অনিয়ন্ত্রিত ঋণ, অযৌক্তিক খরচ ইত্যাদি। এগুলো হয়তো জনপ্রিয়তা আনে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতিকে দুর্বল করে। লাতিন আমেরিকার বহু দেশে এই সমস্যা প্রকট হয়েছে।
অপরদিকে, গণতন্ত্রে সরকার পরিবর্তনের কারণে নীতির ধারাবাহিকতা থাকে না। একটি সরকার যে প্রকল্প শুরু করে, পরবর্তী সরকার তা বাতিল করে দেয় রাজনৈতিক প্রতিশোধ হিসেবে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। অথচ চীন কিংবা সিঙ্গাপুরের মতো রাষ্ট্রগুলোতে যেখানে গণতন্ত্র নেই, সেখানে দীর্ঘমেয়াদি নীতি অনুসরণ করে টেকসই উন্নয়নের উদাহরণ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।
গণতন্ত্র না থাকলে কী বিকল্প?
তবে প্রশ্ন হলো, গণতন্ত্র যদি ঝুঁকিপূর্ণ হয়, তবে বিকল্প কী? একনায়কতন্ত্র, সামরিক শাসন বা রাজতন্ত্র ইতিহাসে বারবার ভয়ংকর প্রমাণিত হয়েছে। জনগণের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়ে শৃঙ্খলা আরোপের নামেই হয়েছে দমন-নিপীড়ন। তাই গণতন্ত্রের দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এটি এখনো তুলনামূলক গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা।
কিন্তু আজকের বিশ্বে গণতন্ত্রকে নতুনভাবে সাজাতে হবে। শুধু নির্বাচন নয়, গণতন্ত্রকে হতে হবে জবাবদিহিমূলক। স্বচ্ছ নির্বাচন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, সুশাসন ও দক্ষ প্রশাসন ছাড়া গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না।
উপসংহার
বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতন্ত্র নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জের মুখে। তবে একে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সমাধান নয়। বরং গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। গণতন্ত্র ঝুঁকিপূর্ণ নয়—ঝুঁকিপূর্ণ হলো এর অপব্যবহার, ভাঙা কাঠামো ও দুর্বল নেতৃত্ব। তাই বিশ্বকে এখন ভাবতে হবে কীভাবে গণতন্ত্রকে সময়োপযোগী করে রাষ্ট্র পরিচালনায় সত্যিকারের কল্যাণমুখী করা যায়।
স্বপন বিশ্বাস
সাংবাদিক ও কবি
শালিখা মাগুরা