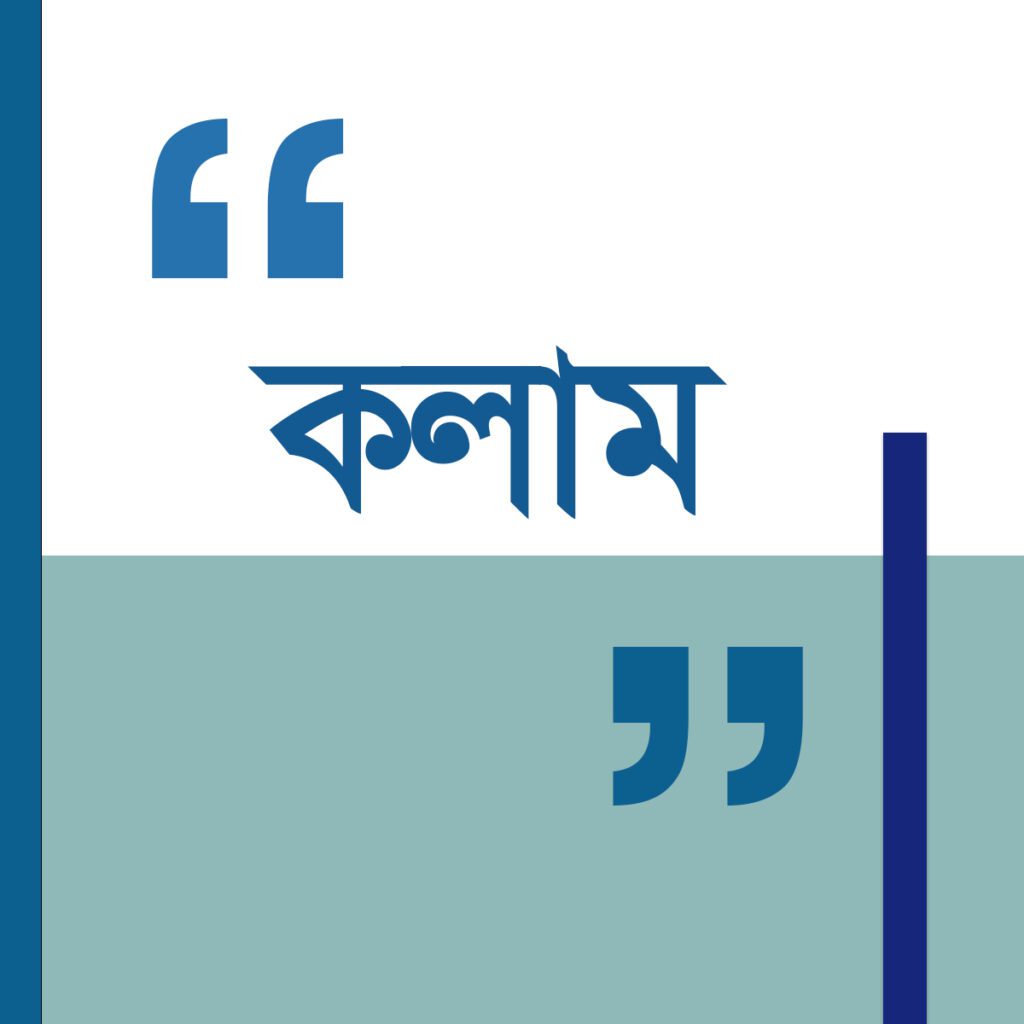
শোয়েব সাম্য সিদ্দিক
শুরুতেই প্রশ্ন: এখন কেন পিআর?
জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যখন রাজনীতির ময়দান উত্তপ্ত, তখন হঠাৎ করে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতি। কেউ বলছেন, ‘‘এটা গণতন্ত্রের পরিপক্ব রূপান্তর’’, আবার কেউ বলছেন, ‘‘এ এক বিপজ্জনক বিভ্রান্তি’’। সরকারের ঘনিষ্ঠ মহলে আচমকা পিআর নিয়ে তৎপরতা ও জনসংযোগের ঝড় উঠায় মনে প্রশ্ন জাগে: ঠিক এমন সময়েই কেন এত আলোড়ন? দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় যখন নির্বাচনের স্বচ্ছতা, ভোটাধিকার এবং নিরপেক্ষতার মতো মৌলিক প্রশ্নগুলোরই সমাধান মেলেনি, তখন এক গভীর কাঠামোগত সংস্কার হঠাৎ আলোচনায় আনা কি সত্যিই গণতন্ত্রের জন্য? নাকি এ কেবল ‘‘দৃষ্টি সরানোর কৌশল’’?
পি আর সহজভাবে বুঝি
পি আর বা Proportional Representation এমন একটি ভোট পদ্ধতি, যেখানে দলগুলো সংসদে আসন পায় তাদের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হিসেবে। অর্থাৎ, যে দল জাতীয়ভাবে যত ভোট পাবে, তারা সেই অনুপাতে আসন পাবে।
একটি সাধারণ উদাহরণ ধরা যাক: দেশে যদি ৩০০টি আসন থাকে এবং কোনো দল ৪০ শতাংশ ভোট পায়, তাহলে তারা পাবে ১২০টি আসন। অন্য একটি দল ৩০ শতাংশ পেলে পাবে ৯০টি আসন। এমনকি ৫ শতাংশ ভোট পেলেও ১৫টি আসন মিলতে পারে। এতে ছোট দল ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়।
এ পদ্ধতির মাধ্যমে ভোটের মূল্য বৃদ্ধি পায়, কারণ একটিও ভোট ‘‘নষ্ট’’ হয় না। তবু প্রশ্ন থাকে, আমাদের দেশে যেখানে ভোটার তালিকা নিয়েই হাজারো বিতর্ক, সেখানে ভোট শতাংশের হিসাবই বা কতটা গ্রহণযোগ্যভাবে হবে?
যাদের সমর্থন রয়েছে
পি আর পদ্ধতির সবচেয়ে বড় শক্তি হলো, কোনো ভোট নষ্ট হয় না। প্রতিটি ভোটেরই সাংবিধানিক প্রতিফলন ঘটে। এতে সংসদে বৈচিত্র্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর প্রবেশ করে, যেমন: সংখ্যালঘু, নারী, প্রান্তিক ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল। বড় দলের একক আধিপত্য কিছুটা কমে যায়, আর দলগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে সমঝোতা ও জোট গঠনের মাধ্যমে সরকার চালাতে হয়।
এক কথায়, এ পদ্ধতিতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন আসে: একটি শক্তিশালী, স্থিতিশীল সরকার ও বিচিত্র মতবাদের ঠাসা, জোটনির্ভর দুর্বল সরকারের মাঝে ভারসাম্য আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিতে পারবে কি?
যাদের আপত্তি রয়েছে
বড় দলগুলো মনে করে পিআর ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এতে একক সরকারের গঠন কঠিন হয়ে পড়ে এবং জোট সরকারের ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা বাড়ে। আমাদের বাস্তবতায় মনোনয়ন বাণিজ্য, দলীয় কোন্দল এবং হাইকমান্ড নির্ভরতা আরও বেড়ে যেতে পারে। এছাড়া, সরাসরি ভোটার-এমপি সম্পর্ক শিথিল হয়, যা গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতায় ব্যাঘাত ঘটায়।
মনে রাখতে হবে, অনেক সময় পিআর পদ্ধতি এমন নেতাদের সংসদে নিয়ে আসে যাদের জনগণ চিনেই না। দলীয় তালিকাভুক্ত এই প্রতিনিধিরা ‘অফিসিয়ালি’ সংসদে থাকলেও জনগণের সঙ্গে কোনো জবাবদিহিমূলক সম্পর্ক থাকে না। ফলে হাইকম্যান্ডই হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা।
মূল বিতর্কের মূলে কী?
বিতর্কটা মূলত সময় ও প্রক্রিয়া নিয়ে। জাতীয় নির্বাচন বাকি মাত্র কয়েক মাস। এমন সংবেদনশীল মুহূর্তে, জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনাহীনভাবে নির্বাচন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন কোনো দায়িত্বশীল সরকারের আচরণ হতে পারে না।
অনেকে আশঙ্কা করছেন, এটি একটি ‘কৌশলগত বিতর্ক’, যা সত্যিকার ভোটের লড়াই থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা হতে পারে।
দাঁড়ায়। ব্র্যাকের একটি জরিপ অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৮০% নাগরিক মনে করেন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রয়োজন, যা জনগণের প্রকৃত মতামত প্রতিফলন করে। (BRAC Institute of Governance and Development, Survey 2023). যে মুহূর্তে দেশের ৮০ ভাগ মানুষ আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য করতে চায়, সেই মুহূর্তেই বিতর্ক উস্কে দিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ঘুরিয়ে দেওয়া কাকতালীয় হতে পারে না। এটি যেন ‘‘গণতন্ত্রের চালাকি সংস্করণ’’ হয়ে না
রাজনৈতিক মাঠের সবচেয়ে বড় দলটি উদ্বিগ্ন কেন?
তারা মনে করে, পিআর বিতর্ক উসকে দিয়ে সরকার আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের মৌলিক প্রশ্ন অর্থাৎ ভোটাধিকার ও নিরপেক্ষতা থেকে ফোকাস সরাতে চাইছে। তারা বলছে, জনগণের রায়কে পাশ কাটিয়ে কোনো অস্থায়ী প্রশাসন নির্বাচনী কাঠামো পাল্টাতে পারে না।
দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে একাধিকবার বলা হয়েছে, ‘‘নির্বাচন আগে, তবে ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতা অগ্রাহ্য করে নয়।’’ শুরু থেকেই তাদের দলীয় হাইকমান্ড একটি সর্বজনগ্রাহ্য, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ওপর জোর দিচ্ছে। তাদের মতে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে কোনো সংস্কার হতে হবে নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে।
বিএনপির এই অবস্থান শুধু রাজনৈতিক নয়, কৌশলগতও। তারা চায়, প্রথমে হোক ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, তারপর আলোচনা হোক কাঠামোগত সংস্কার নিয়ে। কারণ, যদি নির্বাচনের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন থাকে, তবে তার ভিত্তিতে তৈরি কোনো ব্যবস্থা কখনোই টিকবে না।
যেসব দেশে চলছে, যেসব দেশে ব্যর্থ হয়েছে
সফল উদাহরণ:
জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, নেপাল, শ্রীলঙ্কা—এসব দেশে পিআর পদ্ধতি চলছে, তবে রাজনৈতিক ঐক্যমত্য ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলার কারণে এসব দেশে তা কার্যকর।
ব্যর্থ উদাহরণ:
ইসরায়েল: স্বাধীনতার পর থেকে গড়ে আড়াই বছর অন্তর সরকার ভেঙেছে। ২০২১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে মাত্র এক বছরে ৫টি জাতীয় নির্বাচন হয়েছে।
ইতালি: ১৯৪৬ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত ৫০ বছরে ৬০টির বেশি সরকার পরিবর্তন হয়েছে; গড় আয়ু মাত্র ১১ মাস।
বেলজিয়াম: ২০১০ থেকে ২০১১ সালে ৫৪১ দিন সরকারবিহীন অবস্থায় থেকেছে, যা বিশ্ব রেকর্ড।
গ্রীস: অর্থনৈতিক সংকটের সময় পিআর জোট সরকার ব্যর্থ হয়েছিল।
অস্ট্রিয়া: বারবার সরকার ভেঙে যাওয়ায় দেশটি পরে মিশ্র পদ্ধতির দিকে ফিরে যায়।
এসব উদাহরণ বলছে, পিআর কেবল একটি পদ্ধতি নয়, এটি একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যা গড়ে তুলতে সময় ও ঐকমত্য লাগে। আমাদের দেশে যেখানে বাজেট প্রণয়নেও সংসদ সদস্যদের মতামত উপেক্ষিত, সেখানে বহু কণ্ঠস্বরের সরকার কেবলই নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পারে।
বাংলাদেশে পিআর কি সম্ভব?
পিআর সম্ভব, তবে তা ধাপে ধাপে, প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে এবং রাজনৈতিক ঐকমত্যে। বিভক্ত রাজনীতির বাস্তবতায় এটি হঠাৎ চাপিয়ে দিলে অস্থিরতা ও অবিশ্বাসই বাড়বে। এখন এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক পরিবেশ প্রস্তুত নয়, বিশেষ করে একটি অস্থায়ী বা বিতর্কিত সরকারের পক্ষ থেকে এমন সংস্কার গ্রহণযোগ্য নয়।
যারা এখন পিআর বিতর্ক সামনে এনেছে, তারা কি আদৌ এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত জটিলতা বোঝে? নাকি এটা কেবল রাজনৈতিক নজর ঘোরানোর এক অভিনব রাস্তা মাত্র?
সারকথা
পি আর পদ্ধতি যতই উন্নত হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাড়াহুড়ো করে এটি চাপিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এখন আমাদের দরকার ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, এবং জনগণের বিশ্বাস অর্জন। গণতন্ত্রকে টেকসই করতে হলে গণতান্ত্রিক সংস্কার হতে হবে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে, তড়িঘড়ি প্রশাসনিক কৌশলে নয়।
যারা এখন পিআর বিতর্ক সামনে আনছেন, তাঁদের বোঝা উচিত—‘‘গণতন্ত্র শুধুমাত্র গণনাযোগ্য ব্যালটের গাণিতিক হিসাব নয়, বরং জনগণের আস্থা ও সম্মতির মাধ্যমে গড়ে ওঠে। ভোট নয়, সম্মতি ছাড়া কোনো সংস্কার টিকে থাকতে পারে না।’’
লেখক: গণমাধ্যম বিশ্লেষক
shammo4n@gmail.com
