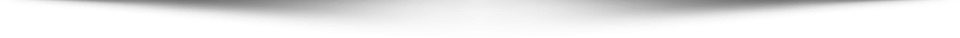দেশে প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলকভাবে চালু হলো স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা ‘স্টারলিংক’। সোমবার (২০ মে) থেকে এই সেবা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের তথ্যমতে, নন-জিওস্টেশনারি অরবিট (NGSO) নীতিমালার আওতায় এই পরিষেবা শুরু হয়েছে।
স্টারলিংক ব্যবহারকারীদের জন্য দুটি প্যাকেজ চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে ‘রেসিডেন্স’ প্যাকেজে মাসিক খরচ ৬ হাজার টাকা, আর ‘রেসিডেন্স লাইট’-এর জন্য খরচ ৪ হাজার ২০০ টাকা। তবে শুরুতেই এককালীনভাবে ৪৭ হাজার টাকা দিয়ে ইন্টারনেট সেটআপ যন্ত্রপাতি (ডিশ, রাউটারসহ আনুষঙ্গিক ডিভাইস) কিনতে হবে। এই সেবায় রয়েছে ডেটা ব্যবহারে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই—অর্থাৎ আনলিমিটেড ডেটা ব্যবহার করা যাবে এবং প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ৩০০ মেগাবিট গতির ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যাবে।
তবে এক জায়গায় একবার বসানো হলে সেই ডিভাইস অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যাবে না—এমন বিধিনিষেধ থাকলেও, সেটআপের অবস্থান থেকেই নিরবিচারে উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে বলে জানানো হয়।
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ জানিয়েছে, দেশের মাত্র ৩০ শতাংশ মোবাইল টাওয়ারে এখনো ফাইবার সংযোগ রয়েছে। বাকিগুলো ‘লো ক্যাপাসিটি’ মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল, যা দিয়ে হাজারো গ্রাহককে সীমিত ব্যান্ডউইথে সেবা দিতে হয়। স্টারলিংক সেই সংকট কাটিয়ে দিতে পারে। এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও অবকাঠামোবিহীন এলাকাতেও সংসদ ভবন বা মন্ত্রীর অফিসের মতোই দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহার সম্ভব হবে।
স্টারলিংক উদ্যোক্তাবান্ধব হতে এমনভাবে নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে যাতে একজন ব্যক্তি বা উদ্যোক্তা চাইলে নিজ খরচে বা সমবায় পদ্ধতিতে ইন্টারনেট সেটআপ কিনে নিজের গ্রাম বা পাড়ায় সেবা দিতে পারেন। ২০ থেকে ৫০ মিটার পর্যন্ত ওয়াই-ফাই রেঞ্জ থাকায় একটি দোকান, হাট বা গ্রোথ সেন্টারে অনেকেই একই সংযোগ ব্যবহার করতে পারবেন।
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব জানান, “আমরা চাই উদ্যোক্তারা যেন এটিকে ব্যবসায়িক মডেল হিসেবে নিতে পারেন। কয়েকজন মিলে একটা তহবিল করে যদি একটি স্টারলিংক সেটআপ কেনেন, তাহলে তারা তাদের এলাকায় ইন্টারনেট সেবা সরবরাহ করতে পারবেন। আইনেও এর কোনও বাধা রাখা হয়নি।”
তিনি আরও জানান, “আমরা একসময় ‘ফোন লেডি’ কনসেপ্টে অভ্যস্ত ছিলাম। এবার ‘ওয়াই-ফাই লেডি’ ধারণা চালুর উদ্যোগ নিচ্ছি। গ্রামীণ নারীরা চাইলে মাইক্রোক্রেডিট বা সহজ কিস্তিতে স্টারলিংক সেটআপ নিয়ে স্থানীয়ভাবে ইন্টারনেট সেবা দিতে পারবেন।” এ বিষয়ে মাইক্রোক্রেডিট কর্তৃপক্ষ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা চলছে।
ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীরাও এই সেবা ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন, একটি আবাসিক ভবনের কয়েকটি ফ্ল্যাট মিলে একটি সংযোগ শেয়ার করে মাসিক খরচ ভাগ করে নিতে পারবেন। যেহেতু স্টারলিংক ডিভাইসে বিল্ট-ইন রাউটার আছে, তাই আলাদা করে আইএসপি নেটওয়ার্কেও যুক্ত করা সম্ভব।
ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, “হ্যাঁ, স্টারলিংকের দাম তুলনামূলক বেশি, তবে আমরা দরকষাকষির মাধ্যমে কিছুটা কমাতে পেরেছি। এবং যেহেতু এটি শেয়ার করা যাবে, বিক্রিও করা যাবে—তাই এটি একটি লাভজনক উদ্যোক্তা মডেল হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।”
এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাঠকরা সহজেই স্টারলিংকের সেবা, খরচ, ব্যবহার পদ্ধতি এবং সম্ভাব্য উদ্যোক্তা মডেল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবেন। চাইলে আপনি এই প্রতিবেদনটিকে গ্রাফিক্স, চিত্র বা ফ্যাক্টবক্স যুক্ত করে আরও তথ্যবহুল করে তুলতে পারেন।